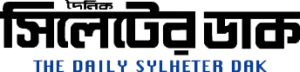আমার পিতা মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
সিলেটের ডাক প্রকাশিত হয়েছে : ২৩ জুন ২০২৩, ১১:২০:৩৩ অপরাহ্ন
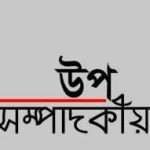
চৌধুরী মুফাদ আহমদ:
আমার পিতা মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর মৃত্যুর ২৯ বছর হলো এই ২৩ জুনে। এই প্রথম তাঁর স¤পর্কে আমি কিছু লিখতে বসেছি। আমি আমার বাবার স¤পর্কে কম আলোচিত একটি বিষয়ে লিখব।
আমার আব্বা একজন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত থাকলেও চাকুরী জীবনে তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৩১ সালে সিলেট এম. সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স করার পর, গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই তিনি শিক্ষা বিভাগে চাকরি শুরু করেন এবং ১৯৭০ সালে রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় শিক্ষা পরিদর্শকের পদ থেকে অবসরে যান। সরকারি চাকরি অনেক সময় মানুষের মধ্যে একটা আনুগত্যভাব তৈরি করে। যাঁরা চাকরির সুযোগ নিয়ে নানা প্রাপ্তিযোগের ধান্ধায় থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই আনুগত্যের মাত্রা আরো তীব্র থাকে এবং নানাভাবে তারা সরকারের প্রতি তাঁদের এই আনুগত্য প্রদর্শন করতে পছন্দ করেন।
আমার বাবা কখনও রাজনীতিতে স¤পৃক্ত হননি এবং কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁর কোন অনুরাগ ছিল না। কিন্তু তিনি কখনও কোন সরকারের প্রতি বাড়তি আনুগত্য দেখাননি এবং নানাসময় চাকরির তোয়াক্কা না করে নীতির প্রশ্নে অনড় ছিলেন।
১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের আগে থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এ নিয়ে মতভেদ ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উর্দুর পক্ষে পাকি সরকারের পক্ষপাতের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। এসময় সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ ছিল সিলেটের বিদ্বৎ সমাজের জন্য শিল্পসাহিত্যচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।
১৯৪৭ সালের নভেম্বরে, আমার পিতা কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের এক সাহিত্য সভায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে লেখা প্রথম দুয়েকটি প্রবন্ধের একটি। এতে তিনি সরাসরি বাংলাভাষার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে লিখেন:
‘পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন ভাষা গৃহীত হইবে এ নিয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক আমাদের নাই। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন হইতে পারে না। বাংলাদেশে উর্দু স্কুল স্থাপন করিয়া আমাদের ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করিতে আমরা কোন অবস্থায়ই দিতে পারিব না। নিজের দেশে পরদেশী হইয়া থাকিব ইহা ভাবিতেও আমাদের লজ্জা বোধ হয়।’
সিলেটে মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশ সরকারের মনোভাব আঁচ করতে পেরে উর্দুর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থানকারীদের নানা সভা-সমিতিতে আক্রমণ চালাতো। সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কাকে নাকচ করে দিয়ে আমার বাবা কেবল প্রবন্ধই লিখেননি, এসব সভা-সমিতিতে যোগ দিয়েছেন। বাংলার পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন।
২
ইতিহাসের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য ছিল আমার পিতার মূল আগ্রহের বিষয় । তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত। মুসলিম সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে একটি রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। আমার বাবা সেই সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। আমার মনে আছে স্কুলে পড়ার সময় আমি যখন নানা ডিকেটটিভ নভেল, নীহাররঞ্জন-বিমল মিত্র-ফালগুনী-তে নিমজ্জ, তখন একদিন আমার বাবা আমাকে রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম খ- বের করে ‘বৌ ঠাকুরাণীর হাট’ পড়তে দিলেন, সেটি শেষ হলেন পড়তে দিলেন ‘রাজর্ষি’, তারপর ‘নৌকাডুবি’, আরেকদিন বের করে দিলেন ‘কণিকা’ কাব্যগ্রন্থ। এভাবে আমার বাবার হাত ধরে আমার রবীন্দ্রসাহিত্যে হাতেখড়ি হয়। শুধু আমি নই আমার পুরো পরিবারেই একটি রবীন্দ্রচর্চার আবহ তৈরি হয় আমার পিতার প্রভাবে। আমার চাচাতো ভাই এবং ষাটের দশকের সুনামগঞ্জের তুখোড় বামপন্থী ছাত্রনেতা চৌধুরী মনসুর আহমদের একসময় পুরো সোনার তরী কাব্যগ্রন্থ এবং সঞ্চয়িতার অনেকগুলো কবিতা মুখস্থ ছিল।
আমার পিতার উত্তরসূরী হিসেবে আমার এই ভাইয়ের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গানের ও গীতিনাট্যের জগতে আমার বিচরণ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এই আলোচনা পরবর্তী একটি প্রসঙ্গের গৌড়চন্দ্রিকা।
ষাটের দশকের প্রথম দিকেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের ১৭ টি জেলার জন্য ১৭ টি জেলা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি হয়। আব্বা সিলেটের প্রথম জেলা শিক্ষা অফিসার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সালে আব্বা ময়মনসিংহের জেলা শিক্ষা অফিসার পদে বদলী হন। ময়মনসিংহে তখন একটি শক্তিশালী বিদ্বৎ সমাজ ছিল এবং উন্নত সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ছিল। আব্বা ময়মনসিংহে বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নানা সভা-সমিতিতে, প্রেসক্লাবে যেতেন। সভা-সমিতিতে যাওয়ার মতো বয়স আমার তখন হয়নি এবং আমার আব্বার ভুমিকা স¤পর্কেও জানতাম না।
বহুদিন পর, আমার আব্বার মৃত্যুর বছর এগারো পর ২০০৫ সালে একদিন তবারক ভাইকে (সাংবাদিক-এডকোকেট তবারক হোসেইন) ফোন করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন অধ্যাপক যতীন সরকার তাঁর ‘পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন’ বইতে আমার বাবা স¤পর্কে কী লিখেছেন দেখেছি কিনা। আমি বইটি সংগ্রহ করে দেখি যাটের দশকের ময়মনসিংহে আমার পিতার এক ঋজু ও গৌরবজনক ভূমিকার কথা লিখেছেন অধ্যাপক যতীন সরকার। বইটি থেকে কিছু উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না:
‘ষাটের দশকের প্রায় গোড়া থেকেই মুসলিম চৌধুরী ছিলেন ময়মনসিংহের জিলা শিক্ষা অফিসার। শ্রীহট্ট-সন্তান এই সুরসিক ভদ্রলোক প্রায় এক দশক ময়মনসিংহে ছিলেন। এমন বিদগ্ধ সাহিত্যপ্রাণ অমায়িক ও উদার হৃদয় মানুষ খুবই কমই দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতার প্রায় পুরোটাই তাঁর মুখস্ত ছিল। নানা আলোচনা সভায় সিলেটি উচ্চারণে মুসলিম চৌধুরীর রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি হতো খুবই উপভোগ্য। এমন একজন রবীন্দ্রপ্রেমিক সরকারি কর্মচারীকে পেয়ে ষাটের দশকে সেই বিরূপ সময়টিতে আমাদের খুবই সুবিধা হয়েছিল।’ (পৃষ্ঠা-৩০৭)
কিন্তু কেন সেটি একটি বিরূপ সময় ছিল? আমাদের মনে রাখতে হবে ষাটের দশকে আইয়ুব খানের সরকার বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি বিরোধী নানা অবস্থান গ্রহণ করে এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের এক নম্বর টার্গেট। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় পাকিস্তান রেডিও রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ রাখে। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন পাকিস্তানের আদর্শের সঙ্গে না মিললে রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেবার ঘোষণা দেন। এর পর বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাও রবীন্দ্রবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং অনেক নামী-দামী কবি-সাহিত্যিক সরকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বক্তব্য দেন। তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে তা ছিল অনেক শক্তিশালী।
যতীন সরকার লিখেছেন যে সভা-সমিতিতে আব্বা রাজনৈতিক বক্তৃতা করতেন না। কিন্তু তিনি সংস্কৃতির প্রশ্নে তাঁর যে পরিষ্কার অবস্থান ছিল সেটি ব্যক্ত করতে তিনি কখনও পিছিয়ে যাননি। যতীন সরকার লিখেছেন:
‘পঁয়ষট্টি পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে উনিশ শো উনসত্তরের ফেব্রুয়ারি (আব্বার ক্ষেত্রে আটষট্টি সাল)-এই ক’বছরে ময়মনসিংহ শহরে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেদের নানাভাবে জড়িয়ে রেখেছিলেন মুসলিম চৌধুরী ও কবীর চৌধুরী। এরা দুজনেই সরকারি কর্মচারি হলেও পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক ভাবদর্শের বিপরীত ভূমিতেই ছিল এদের অবস্থান। ময়মনসিংহের প্রায় সব সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনের সঙ্গে এরা যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।’ (৩০৮)
একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে আব্বার যে সাংস্কৃতিক অবস্থান ছিল তা যে সবাই পছন্দ করেছিলেন তা নয়। কেউ কেউ আব্বাকে একটু সাবধানে কথাবার্তা বলতে অনুরোধ করতেন।
৩
নীতির প্রশ্নে আমার বাবার দৃঢ়চিত্ততার সর্বশেষ ঘটনাটি যা এখানে উল্লেখ করব সেটি ময়মনসিংহে ১৯৬৮ সালের ঘটনা। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খান ছিলেন ময়মনসিংহের লোক। ১৯৬৭ সালের রবীন্দ্র-বিতর্কের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তিনি রবীন্দ্রসংগীত লেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁরই নিজের জেলার জেলা শিক্ষা অফিসারের রবীন্দ্রপ্রীতিতে ক্ষুব্ধ ছিলেন কি-না জানিনা, কিন্তু তাঁর সঙ্গেই আব্বার টক্কর লাগলো।
এ স¤পর্কে আব্বার নিকট থেকে আমরা কিছু শুনেছিলাম। দীর্ঘদিন পর আমার কর্মসূত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ একাডেমি (ঘঅচঊ) -এর অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিজ এর সঙ্গে পরিচয় হয়। যেকোনভাবে তিনি আমার পিতৃপরিচয় পেয়ে আমাকে বলেন যে আমার আব্বার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানের বচসার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের একজন নবীন প্রভাষক। আমার অনুরোধে ঘটনাটি তিনি আমাকে লিখেও পাঠান।
ঘটনাস্থল ছিল ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস। মোনায়েম খান প্রায়ই ময়মনসিংহ আসতেন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করে তাদের ধমকাধমকি করতেন। সেদিন বিভিন্ন স্কুলের সরকারি বরাদ্দ দেয়া নিয়ে মোনায়েম খান জানতে চাইলে আব্বা তালিকা ধরে জানাতে থাকেন কোন কোন স্কুলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মোনায়েম খানের ভাই খোরশেদ খান, যিনি নিজেকে ময়মনসিংহের গভর্ণর বলতেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এক পর্যায়ে বাজিতপুরে তাঁর স্কুলে কেন বরাদ্দ দেয়া হয়নি তা জানতে চান। যে নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দ দেয়া হয়েছে আব্বা বিনয়ের সাথে তা ব্যাখ্যা করলেও তিনি তা বুঝতে চান না এবং স্বয়ং গভর্ণর বলা সত্ত্বেও সেই স্কুলে বরাদ্দ না দেয়াটাকে তিনি তাঁর ও গভর্নরের জন্য অপমানজনক বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু নীতিমালার ব্যতিক্রম করার লোক তো মুসলিম চৌধুরী ছিলেন না! এক পর্যায়ে মোনায়েম খান বলেন- জানেন আমি আপনার চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারি? একথা শুনে আব্বা বলেন, না সেটি আপনি পারেন না। তখন মোনায়েম খান বলেন, আমি আপনাকে এখনই বদলী করতে পারি। আব্বা জবাব দেন, হ্যাঁ, তা পারেন এবং আমি তার জন্য প্র¯ুÍত আছি। ড. আনোয়ারুল আজিজ লিখেছেন, সভায় উপস্থিত সকলেই নিশ্চুপ। অনাকাঙ্খিত কোন কিছু ঘটার আশংকায় শুধু একে অপরের দিকে মুখ চাওয়াচায়ী করছিলেন। মুসলিম চৌধুরীর সাহস ও মনোবল দেখে বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তাগণ বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন।
পর দিন টেলিগ্রামের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক অবমুক্তিসহ আব্বাকে কুষ্টিয়ায় বদলী করা হয়। ময়মনসিংহের নাগরিক সমাজ বিদায় সংবর্ধনা দিতে চাইলে আমার বাবা বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করে সেদিন রাতের ট্রেনেই কুষ্টিয়া রওনা হন। কিছুদিন পর আমরা সিলেট চলে আসি।
আমার বাবা এসব ঘটনা নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতেন না। এমনকি মোনায়েম খানের এই আচরণের জন্য কোনদিন মোনায়েম খানকে দোষারোপ করতেও শুনিনি। সংসারের নানা তুচ্ছ ঘটনার উর্ধ্বে ওঠার এক সাত্ত্বিক ক্ষমতা ছিল আমার বাবার।
লেখক: প্রাবন্ধিক, সাবেক অতিরিক্ত সচিব