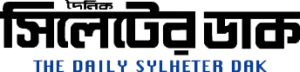মার্কিন-চীন : সংঘাত কী অনিবার্য
সিলেটের ডাক প্রকাশিত হয়েছে : ২৫ জুন ২০২৩, ৩:২২:৫৮ অপরাহ্ন
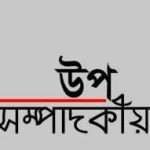
অ্যাডভোকেট আনসার খান
বিশ্বব্যবস্থা সম্প্রতি একটি নতুন ক্রান্তিকালে প্রবেশ করেছে, ক্ষমতার দুটি কেন্দ্র, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বিশ্বশক্তির আধিপত্যের স্থানটি দখল করার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। এই দুটি দেশের বর্তমান সম্পর্কের অবনতি ও সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকার কারণে বৈশ্বিক ব্যবস্থা ইতিমধ্যে-ই গভীর পরিনতির সম্মুখীন হয়েছে।
২০২০ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের আধিপত্যের জন্য লড়াই অবশেষে বিশ্বব্যবস্থাকে সামরিক সংঘাতের দিকে নিয়ে যাবে। ‘আমরা খুব বিপজ্জনক দিকে আগাচ্ছি’-মন্তব্য করেছিলেন মি: গুতেরেস।
যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক আধিপত্যের জন্য একটি সীমাহীন প্রতিযোগিতা কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি নতুন যুগ হিসেবে শুরু হয়েছে। যদিও অনেকগুলো মূল সূচকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতি, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্র এখনও চীনের থেকে এগিয়ে আছে।
দেশ দুটির মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতাকে বিশ্লেষকগণ ‘দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধ’ হিসেবে দেখছেন। মাইকেল ডয়েল তার ‘কোল্ড পিস : এভয়েডিং দ্য নিউ কোল্ড ওয়ার’ বইয়ে লিখেছেন, ‘আমরা আরেকটি শীতল যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে আছি এবং বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য গুরুতর প্রভাব সহ।’
উল্লেখ্য, ১৯৪৫ সালের পরবর্তী ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রথম স্নায়ুযুদ্ধটি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিলো। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনের মধ্যদিয়ে ওই স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিলো এবং দ্বি-পোলার বিশ্বব্যবস্থার স্থলে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিলো, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিলো বিশ্বের একক মোড়ল। কিন্তু একুশ শতকে চীন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক শক্তির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সামনে এসেছে। ফলে দুই শক্তির মধ্যে ঠান্ডাযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
ইন্দো-প্যাসিফিক একটি নতুন স্নায়ুযুদ্ধের সম্ভাব্য আনুষ্ঠানিক সূচনা বিন্দু বলে মনে করেন পর্তুগিজের সাবেক প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাওলো পোর্টাস। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির একজন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হ্যাল ব্র্যান্ডস এবং যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পন্ডিত, ইতিহাসবিদ, (যাকে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ‘ডিন অব কোল্ড ওয়ার হিস্টোরিয়ানস’ হিসেবে অভিহিত করেছে,) অধ্যাপক জন লুইস গ্যাডিস যৌথভাবে লিখিত এবং ফরেন পলিসিতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে লিখেছিলেন যে, মার্কিন ও চীন ‘একটি নতুন শীতল যুদ্ধে প্রবেশ করেছে, যার অর্থ হলো একটি দীর্ঘায়িত আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন চীনকে ‘গুরুতর প্রতিযোগী’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বের সামনে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হলো চীন। বলা হয়ে থাকে, এটি চীনা কর্তৃত্ববাদ ও যুক্তরাষ্ট্রের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে একটি সংঘাত ও দ্বন্দ্ব। দেশ দুটির দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতির সীমা ছাড়িয়ে নিরাপত্তা ও সামরিক শক্তির দ্বন্দ্ব তথা বিশ্বব্যবস্থায় আধিপত্য কায়েমের কৌশলগত লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।
বাইডেন প্রশাসনের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘সবচেয়ে পরিনতিমূলক ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ’ হিসেবে বিবেচনা করছে বিধায় দেশটির জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশলে চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘জাতীয় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো শক্তিপ্রদর্শনের মোকাবেলা করার লক্ষ্যে চীনের শি জিনপিং তার সেনাবাহিনীকে ২০২৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণ এবং সমস্ত ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে দেশটি ব্যাপক পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও মজুত করে চলেছে। অর্থাৎ দেশ দুটি পরস্পরের মোকাবেলায় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।
দুটি দেশ-ই অবশ্য প্রতিবছর প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে, যদিও প্রতিরক্ষা ব্যয়ের দিকদিয়ে চীনের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র অনেক বেশী ব্যয় করছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২৩ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে দেখা গেছে ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র এখনও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সামরিক ব্যয়কারী দেশ। ২০২২ সালে মার্কিন সামরিক ব্যয় ৮৭৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা মোট বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়ের ৩৯ শতাংশ। ওই প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যয়কারী চীনের ব্যয়ের চেয়ে মার্কিন ব্যয় তিনগুণ বেশি। ২০২২ সালে চীনের সামরিক ব্যয় ২৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২১ সালের চেয়ে ৪.২ শতাংশ বেশি।
দুটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে এই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা একটি যুদ্ধ এবং এমনকি একটি নতুন বাইপোলার যুগের সূচনা করতে পারে বলে-ও অনেক বিশ্লেষক মনে করেন।
ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক মূল্যবোধ, সমাজ, অর্থনীতি, বানিজ্য এবং প্রযুক্তি পরিচালিত। উভয়-ই একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিস্তৃত সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তি পুঁজির আধিপত্য এবং পরেরটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।
যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কিন ফেয়ারব্যাঙ্ক সেন্টারের পরিচালক মার্ক উ বলেছেন দেশ দুটির সম্পর্কের কেন্দ্রস্থলে বর্তমানের চ্যালেঞ্জ হলো- ‘দুটি সুপারপাওয়ার দেশ একটি কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়’ জড়িয়ে পড়েছে। তার মতে, দেশ দুটির মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শাসনের মডেলের মধ্যে নিবিষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান এবং উভয়পক্ষ-ই নিজেদের মডেলকে সুপিরিয়র হিসেবে প্রচার ও বিবেচনা করে।
বাস্তবতা হচ্ছে, উ, মনে করেন ‘একটি পক্ষ বর্তমান স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করতে চায়, পক্ষান্তরে অন্যটি বিদ্যমান স্থিতাবস্থা সংরক্ষণ করতে চায়।’ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস এটি বলে যে একটি উদীয়মান শক্তি সর্বদা-ই বিদ্যমান আধিপত্য এবং স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে। মার্কিন-চীন সংঘাত এই প্যাটার্ণের মধ্যে পড়ে। কেননা চীন একটি উদীয়মান শক্তি এবং সেটি বিদ্যমান মার্কিন আধিপত্যের স্থলাভিষিক্ত হতে চায়। দুটি শক্তির কৌশলগত মৌলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানে-ই।
বিশ্বব্যবস্থায় আধিপত্য স্থাপনের এই লড়াইয়ে জনগণ কতটুকু সম্পৃক্ত সেটি দেশ দুটির নেতাদের বিবেচ্য নয়। মার্ক উ এইপ্রসঙ্গে বলেছেন, ‘দেশ দুটির নাগরিকদের সিংহভাগ এক-ই জিনিস চায়; বস্তুগত নিরাপত্তা, শারীরিক নিরাপত্তা, সূযোগ এবং সন্তানদের জন্য একটি ভালো, উন্নত ভবিষ্যত।’ জনগণের এই চাওয়াটি বরাবর উপেক্ষিত হয়ে আছে রাষ্ট্রনায়কদের কাছে। রাষ্ট্রগুলো এখন ক্ষমতা প্রক্ষেপনে ব্যস্ত। জনগণের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে দেশ দুটি মূলত বিশ্বব্যবস্থায় আধিপত্য বজায় রাখা বা আধিপত্য কায়েমের কৌশলগত লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে, যা বিশ্ববাসীকে একটি পারমাণবিক যুদ্ধ তথা ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন,-দুই বৃহৎ শক্তির আধিপত্য স্থাপনের কৌশলগত লড়াইয়ের কারণে বিশ্বব্যবস্থা একটি যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন। উভয়পক্ষ পরস্পরের, একে অন্যের রেডলাইনের খুব কাছাকাছি থাকার কারণে যেকোনো সময় রেডলাইন অতিক্রম করার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে বিশ্লেষকদের অভিমত। রেডলাইন অতিক্রম করার মানে খুব-ই বিপজ্জনক, যা শুধু দুটি পক্ষকে-ই নয়, অপরিবর্তনীয়ভাবে গোটা বিশ্বব্যবস্থাকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে।
ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ নেইল ফারগুসনের সাথে দেওয়া এবং স্প্যানিস পত্রিকা ‘দ্য এল মুন্ডো’তে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব ও সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, ‘ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে একটি যুদ্ধ, বিপর্যয়কর, মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক হবে, যা সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে।’ দূর্ভাগ্যবশত, এটি এখন আর অচিন্তনীয় নয়। উভয় শক্তির মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত অস্থির। উভয় দেশের জন্য একটি মারাত্মক রেডলাইন অতিক্রম করার ক্ষমতা ও আশঙ্কা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম যুক্তরাষ্ট্র ও চীন, শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একে-অপরের মূখোমূখি দাঁড়িয়ে আছে,- এটি-ই ভয়ের কারণ।
উভয় পরাশক্তির কাছে এমন আর্থিক সংস্থান ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সক্ষম পারমাণবিক ওয়ারহেড সহ ভয়ংকর প্রযুক্তি ও মারণাস্ত্র রয়েছে, যা অতীতের সময়গুলোতে ছিলো না। উল্লেখ্য যে, বিবিসি’র প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৩ সালের তথ্য মতে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ৫৪২৮ এবং চীনের অস্ত্রাগারে ৩৫০ পারমাণবিক অস্ত্র মজুত আছে। দুটি দেশের আধিপত্যের প্রতিযোগিতায় পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার মানবসভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। হিরোশিমায় ১৯৪৫ সালে ফেলা পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞ এখনো ভূলতে পারছে না মানবসভ্যতা। বর্তমানে মার্কিন পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র বি-৮৩ মাধ্যাকর্ষণ বোমা হিরোশিমাতে ফেলা বোমার চেয়ে ৮০ গুণ বেশি শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক।
সিঙ্গাপুরের উপপ্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং- এর মতে, বিশ্বের দুটি বৃহত্তম অর্থনীতি ও সামরিক শক্তি, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বিস্তৃত বিভেদ এখন কিছু ক্ষেত্রে অমীমাংসিত বলে মনে হচ্ছে। তাইওয়ান প্রণালী অঞ্চলের ‘সবচেয়ে বিপজ্জনক ফ্ল্যাশপয়েন্ট’ হয়ে উঠার সাথে সাথে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার কারণে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর-ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আমরা ‘প্রান্তের কাছাকাছি চলে যাচ্ছি’ তিনি যোগ করেছিলেন। সিঙ্গাপুরে সাং রিলা ডায়ালগে বক্তব্যদানকালে উপপ্রধানমন্ত্রী এমন মন্তব্য করেছেন।
একুশ শতকের মূল চালিকা শক্তি হলো মার্কিন ও চীনের মধ্যে চলমান প্রতিযোগিতা। দুটি শক্তি স্পষ্টতই বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের ঠান্ডা লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। এই নতুন শীতল যুদ্ধের ডানা বিশ্বের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে। যেমন, বেশ কিছু ঘটনা প্রমাণ করে যে দুটি পরাশক্তি অভ্যন্তরীণভাবে যা কিছু করে না কেন, যেমন- সামরিক, প্রযুক্তিগত বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ, তার সবকিছু তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ে তাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে।
এই নতুন শীতল যুদ্ধকে উত্তপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে পরিণত করার সম্ভাবনা রাখে তাইওয়ান। সেখানে কী যে হয় তা কেবল সময়-ই বলে দেবে। তাইওয়ান প্রশ্নে মার্কিন-চীন, দুটি পরাশক্তি সরাসরি ও মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। এছাড়াও হংকং, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ চীন সাগর, ভারত মহাসাগর সহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে অনেক বড় দ্বন্দ্বের উপসর্গ বিদ্যমান রয়েছে।
এশিয়া আবারও মার্কিন ও চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এশিয়া কেন্দ্রিক শীতল যুদ্ধের ডানা বিশ্বের দেশগুলোকে বিভাজিত করে ফেলছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া,নিউজিল্যান্ড, আসিয়ানভুক্ত কিছু দেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ন্যাটো,ইইউ, এশিয়া প্যাসিফিকের অংশীদার দেশগুলো ক্রমেই যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ে ভীড় করছে এবং অন্যদিকে বেইজিং রাশিয়া, ইরান প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ করে একটি ‘নতুন বিশ্বব্যবস্থা’ পুনর্গঠন করতে চাইছে। এই লক্ষে দীর্ঘ সময়ধরে বিশ্বের এমনসব এলাকা রয়েছে, যেখানে উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক বিনিয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজটি করছে চীন।
দেশ দুটির মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ও প্রতিযোগিতা চলমান থাকাস্বত্তেও আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীন নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছে এবং উভয় দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব দাবি করেছেন যে দেশ দুটির মধ্যে শীতল যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা আপাতত দেখছেন না তারা।
সূত্র : ব্লুমবার্গ, সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট, মাদ্রিদভিত্তিক পত্রিকা-ইল পিএআইএস, বিবিসি নিউজ, ইউনিয়ন অব কনসার্নড সাইন, আল-জাজিরা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা, ফরেন পলিসি, স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
লেখক : আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক।